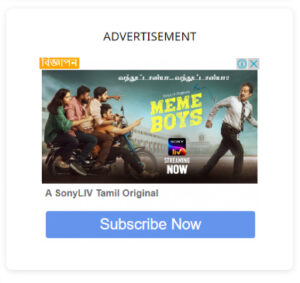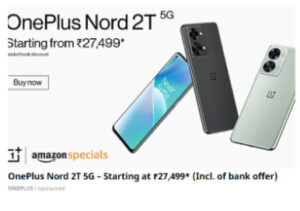- August 13th, 2022
শতবর্ষে সহস্র প্রণতি
সুমন চট্টোপাধ্যায়
‘মনে হয়েছিল দেখেছিনু করুণা তব, আঁখি নিমেষে গেল সে ভেসে’।
সন্তোষ কুমার ঘোষ এর পরেই এমন একটি প্রশ্ন করে বসলেন, আমার ধরণি দ্বিধা হওয়ার অবস্থা। বলো তো দেখি রবীন্দ্রনাথ ‘মনে হয়েছিল’ শব্দ-দু’টি লিখতে গেলেন কেন? দেখেছিনু করুণা তব বললেই তো চলত, অর্থের কোনও তারতম্য হত না।
আমি কিয়ৎক্ষণ মৌনীবাবা হয়ে বসে থাকলাম বাধ্য হয়ে। এমন একটি অদ্ভুত প্রশ্ন কারও মনে জাগতে পারে আমি সেটাই ভাবতে পারি না, উত্তর দেওয়া তো দূরস্থান। প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল, যূপকাষ্ঠে ছাগ-শিশুকে পেয়ে সন্তোষবাবুর আমোদ আরও বেড়ে গেল। তোমার যা মনে হয় সেটাই বলো, চুপ করে বসে থেকো না।’
নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে আমি বলে বসলাম, ‘নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এখানে ‘মনে হয়েছিল’ বসানোটা যুক্তিযুক্ত হবে, তাই বসিয়ে ছিলেন।’
তার পরেই এলো প্রায় রাবীন্দ্রিক সেই সুবচন যা আমাকে আরও অনেকবার শুনতে হয়েছে। ‘তোমার বাবা আমার বন্ধু বলে মনে কোরো না, তোমাকে আমি শুয়োরের বাচ্চা বলতে পারব না।’
হা ঈশ্বর!
আধুনিক বাংলা সাংবাদিকতার স্থপতির শতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে এই বাক্যালাপের প্রসঙ্গটি মনে পড়ে গেল কেন? একটি কারণ মানুষটির নির্বিকল্প রঙিন ব্যক্তিত্বের একটা ঝলক সামনে আনা। দ্বিতীয় কারণ, আমার এই তিন কুড়ি তিন বয়সে সন্তোষ কুমার ঘোষের মতো রবীন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যিনি ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া উপন্যাস ‘শেষ নমস্কার, শ্রীচরণেষু মাকে’ গ্রন্থটি তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে গঙ্গাজলে গঙ্গপুজো সেরেছিলেন। ‘প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে, চিরপথের সঙ্গী আমার চির-জীবন হে।’
সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষকে ভাবীকাল মনে রাখবে, রাখতে বাধ্য হবে। ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘কড়ির ঝাঁপি,’ ‘নানা রঙের দিন’, ‘জল দাও’ কিংবা ‘শেষ নমস্কার’-এর লেখককে উপেক্ষা করে কল্লোল-উত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লেখা অসম্ভব। কিন্তু সাংবাদিক সন্তোষ কুমার ঘোষকে? এই তো তাঁর শতায়ু হওয়ার বছরটি কেটে যেতে চলল এক রকম অলক্ষ্যেই। দু-একটি জোলো লেখা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না তো! সংবাদের সঙ্গে সংবাদের কারিগরের এক আশ্চর্য মিল আছে, উভয়েই ক্ষণস্থায়ী। ভোরের কাগজ বেলা গড়ালে ঠোঙা, কাগজের কারিগর দৃশ্যপট থেকে সরে গেলেই বিস্মৃতির আঁস্তাকুড়ে। এমনতরো বিস্মরণ তাঁর প্রাপ্য কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তবে এটাই হকিকৎ।
বিস্মরণে অবদান অস্বীকৃত থাকতে পারে, মুছে যায় না। একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই জানতে পারা যাবে সন্তোষ কুমার ঘোষ বাংলা সাংবাদিকতায় যে আধুনিক ঘরানার সূচনা করেছিলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা তাই বহন করে চলেছি। সাধুভাষা থেকে চলিতভাষায় রূপান্তর, চটকদার শিরোনাম, সহজ, ঝরঝরে ভাষার ব্যবহার, খেলার খবরকে প্রথম পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা, খবরের ময়দানে সাহিত্যিকদের নামিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি পাঠকের সঙ্গে সংযোগের পোক্ত সেতু-বন্ধন— এ সবেরই প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। আজকে এ সব জলভাতের মতো সহজ মনে হতে পারে, পঞ্চাশের দশকের শেষে বা ষাটের দশকের সূচনায় এই পরিবর্তনের গুরুত্ব ছিল আক্ষরিক অর্থেই বৈপ্লবিক। সন্তোষবাবু মাঠে-ঘাটে ঘুরে সাংবাদিকতা করেননি, অনুজ-প্রতিম গৌরকিশোর ঘোষের মতো তিনি ‘অ্যাক্টিভিস্ট জার্নালিস্ট’ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নেপথ্য-নায়ক প্রধানত যাঁর সৌজন্যে বাংলা সাংবাদিকতা কিছুটা জাতে উঠেছিল, অনেক প্রতিভার উন্মেষের ক্ষেত্রটি তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন।
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলতেন, ‘সন্তোষকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দিলে ও একাই একটা কাগজ বের করে দিতে পারে।’ মানে তিনি ছিলেন একাই একশো, খবরের কাগজে হেন কোনও কাজ নেই যা তিনি জানতেন না বা নিজে অনুশীলন করতেন না। সন্তোষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করা আমার অগ্রজদের মুখে শুনেছি, তাঁর হাতের জাদু-স্পর্শে মামুলি রিপোর্টও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, ঝড়ের গতিতে তিনি সম্পাদনা করতে পারতেন। লেটার প্রেসের যুগে তিনি সারা রাত জেগে দাঁড়িয়ে থেকে পাতা মেক-আপ করতেন। আর সাড়া-জাগানো শিরোনাম? আমার সাত বছর বয়সে পড়া একটি শিরোনাম ছাপ্পান্ন বছর পরে আজও মনে আছে। জওহরলালের মৃত্যুর খবরে সন্তোষবাবু শিরোনাম দিয়েছিলেন, ‘নেহরু নাই, ভারত রত্ন-হীন।’
সন্তোষ কুমার ঘোষই সম্ভবত এ দেশের একমাত্র সাংবাদিক, যিনি একই সঙ্গে দু’টি ভাষার কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন, বাংলা ও ইংরেজি। দু’জন সহকর্মীকে নিজের টেবিলের ওপারে বসিয়ে তিনি অনেকটা মাইকেলের ঢঙে একজনকে বাংলায় অন্যজনকে ইংরেজিতে সম্পাদকীয় ‘ডিকটেট’ করতেন। অনেক পরে তাঁর সহকর্মী হওয়ার সুবাদে আমিও সন্তোষবাবুর অনেক লেখার ডিকটেশন নিয়েছি, দুই ভাষাতেই।
একবারও জিজ্ঞেস না করে নির্ভুল বানানে ইংরেজি ডিকটেশন নিতে পারলে তিনি দারুণ খুশি হতেন। ক্রোধ এবং বাৎসল্য উভয়েই তাঁর আতিশয্য ছিল অতি মাত্রায়। আমার কাছে অবশ্য এগুলো ছিল টিউটোরিয়াল ক্লাস, শুনতে শুনতে, লিখতে লিখতে কত কিছু যে শিখে ফেলেছি! সন্তোষবাবুর স্থির বিশ্বাস ছিল, ভালো বাংলা লেখার আবশ্যক পূর্ব শর্ত হলো ভালো ইংরেজি জানা। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে, বাংলা ভাষার দিকপালদের অনেকেই আসলে ইংরেজির ছাত্র।
কর্মজীবনের গোড়ায় আদর্শ সাংবাদিক হওয়ার শিক্ষা আমি সন্তোষবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। তিনি জোর দিতেন তিনটি বিষয়ের ওপর— উদয়াস্ত পরিশ্রম করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা, সজাগ কৌতূহলী মন আর বই-বান্ধব হওয়া। তিনি নিজেও ছিলেন এই তিন বৈশিষ্ট্যের জীবন্ত উদাহরণ। অবিশ্বাস্য কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রথম যৌবন কেটেছিল, উপার্জনের তাগিদে একসময় তিনি একইসঙ্গে দু’টি কাগজে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, একটিতে দিনের বেলায়, অন্যটিতে রাতে। আমি যখন তাঁর অধীনে কাজ করতে ঢুকি সন্তোষবাবুর কর্মজীবনের সেটা গোধূলিবেলা। তবু হাতে কাজ থাকলে তিনি অশক্ত শরীর নিয়েও দিবারাত্র মগ্ন থাকতে পারতেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পরে তাঁকে নিয়ে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি দীর্ঘ ইংরেজি ফিচার লিখেছিলেন তিনি। সুনীলের সঙ্গে আড্ডা মেরে ফিরলেন মধ্যরাতে, তারপর নিজের ঘরের ছোট্ট ডিভানে ঘণ্টা তিনেক জিরিয়ে নিয়ে শুরু করলেন এক নাগাড়ে ডিকটেশন। ভোরের আলো ফোটার কিঞ্চিৎ আগে লেখা শেষ হলো। কোনও জড়তা নেই, বাধাহীন চিন্তার স্রোত, ইংরেজিটাই যেন তাঁর মাতৃভাষা। অবাক বিস্ময়ে সে রাতে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করেছিলাম।
হাতের কাছে যা পেতেন সেটাই পড়তেন, অতলান্ত পাণ্ডিত্য নিয়ে অনায়াসে তর্কে অবতীর্ণ হতে পারতেন দিগগজ পণ্ডিতদের সঙ্গে। বাংলা বানান নিয়ে সুকুমার সেনের সঙ্গে তাঁর সশ্রদ্ধ বাকযুদ্ধ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানায় নিয়মিত ভাবে অগুন্তি লিটল ম্যাগাজিন আসত, সব ক’টি তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, কারও লেখা ভালো লাগলে ঠিকানা অথবা ফোন নম্বর জোগাড় করে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন। এ ভাবে বাংলা সাহিত্যের অনেক রত্নকে তিনি আবিষ্কার করে একজোট করেছিলেন এক ছাদের তলায়। কোথাও প্রতিভা বা সম্ভাবনার হদিশটুকু পেলে এ ভাবে সাড়া দিতে আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি।
এহেন প্রতিভাধর, পণ্ডিত প্রবর মানুষটি আজকের দিনে কোনও বড় সংবাদপত্রে চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলেই বিবেচিত হতেন না। কেন না অনটনের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ম্যাট্রিকে বাংলায় লেটার পাওয়া ছেলেটি কোনও অনার্স কোর্সে নাম লেখাতে পারেননি, পাস কোর্সে বি এ পাশ করেছিলেন। অবশ্য এ জন্য সন্তোষ কুমার ঘোষের হীনম্মন্যতাবোধ ছিল না, স্বঅর্জিত জ্ঞান, শিক্ষা ও জীবনবোধ সম্পর্কে এতটাই আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর।
আশৈশব চেনার সুবাদে সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের চরিত্র একটু ভিন্ন ছিল, আমি একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয়ই পেতাম। একদিন কথায় কথায় আমি জানতে চেয়েছিলাম, অনার্স পড়লে তিনি কোন বিষয়ে পড়তেন।
‘কেন, ইংরেজি!’ বন্দুকের কার্তুজের মতো বেরিয়ে এল সন্তোষবাবুর উত্তর।
কেমন ফল করতেন মনে হয়?
‘অবধারিত ভাবে ফার্স্ট হতাম। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।’
তাহলে পড়লেন না কেন?
‘আসলে আমাদের ব্যাচে যে বেচারা ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হল, তার ভাত আমি মারতে চাইনি।’
‘কুইন্টেসেনশিয়াল’ সন্তোষ কুমার ঘোষ। শতবর্ষে তাঁকে সহস্র প্রণতি।



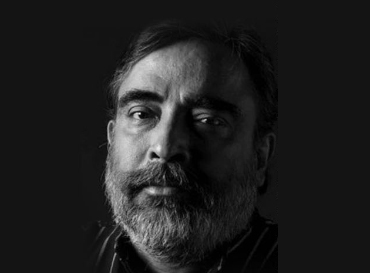
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How