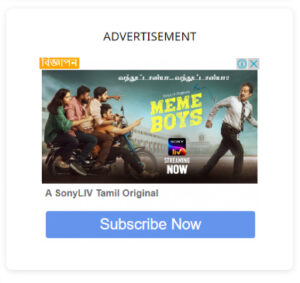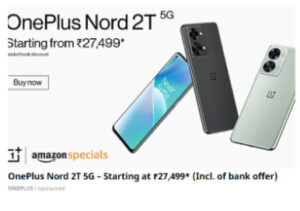- August 13th, 2022
জয় বাবা বিশ্বনাথ
দেবাশিস দাশগুপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হতে তখনও সিকি শতাব্দী দেরি। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পড়তে বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হবে আরও ১৯টি বছর। তারও এক বছর পরে মধুকবি লিখছেন, একেই কি বলে সভ্যতা আর বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ। বিদ্যাসাগর তখনও বাংলা গদ্য রচনায় হাত দেননি। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়নি। তৈরি হয়নি বানানের কোনও ব্যকরণ। ভাষার নবজাগরণে বাংলা তখন হাঁটি হাঁটি পা পা। বলার মতো রয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি আর রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন সঙ্গীত জগতের হলেও রামমোহন গদ্য লিখেছেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। তা সর্বজন প্রণিধানযোগ্য নয়। সম্বল ও সম্পদ বলতে সাকুল্যে এটুকুই। এমন প্রেক্ষিতে সেটুকুই আশ্রয় করে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ ও সাহিত্য রচনা। কোনও বিশেষ প্রয়োজন বা কারণে নয়, নৌকা নিয়ে তিনি অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েছিলেন দেশ, প্রকৃতি, মানুষ দেখবেন বলে। অজানাকে জানার উদগ্র বাসনায় দক্ষিণবঙ্গের কালনা থেকে এ নদী সে নদী হয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন উত্তরবঙ্গের রংপুর। ৩০ দিনের সেই ভ্রমণ তিনি ডাইরির আকারে লিখেছিলেন। তাতে দিন, ক্ষণ, সময়, উল্লেখ ছিল সবেরই। বাংলা গদ্যে প্রথম ভ্রমণ কাহিনিই নয়, ডাইরির ফর্মে লেখা প্রথম কাহিনিও বটে। এর ১২৫ বছর পরে সাহিত্যের এই ফর্মেই আত্মপ্রকাশ প্রফেসর শঙ্কুর ব্যোমযাত্রীর ডাইরি। তবে তা সত্যজিতের কল্পনার ফসল। বিশ্বনাথের সাহিত্য নির্বিকল্প ভাবে কল্পহীন, যার পুরোটাই বাস্তব। বাহুল্য ও আবেগবর্জিত, অতিরঞ্জনের লেশহীন যা কি না তথ্যে সমৃদ্ধ। প্রতিদিনের কাহিনি সংক্ষিপ্ত কিন্তু, তাঁর ভ্রমণপথের প্রতিটি জায়গার নিখুঁত বর্ণনায় অনায়াসে তৈরি করে নেওয়া যায় তৎকালীন নদীপথের মানচিত্র।
পাঠক কল্পনা করুন, ১৮৪০-এ বন-জঙ্গল সাফ করে কলকাতা নগরীর চেহারা নিচ্ছে। আইন-কানুন, জোর যার মুলুক তার। রোগ-কলেরার মতো মহামারী রোজনামচা। এমন সময় ৩০ দিনের নৌ-সফর সহজ ব্যাপার ছিল না। সে ভ্রমণের পদে পদে অনিশ্চয়তা। ডাকাতের ভয়, বন্যপশুর ভয়, দিগভ্রষ্ট হওয়ার ভয়। তার উপর বিশ্বনাথ ছিলেন সাত্বিক ব্রাহ্মণ। ভ্রমণকালীন একাদশী পালনও করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। যাত্রা শেষে নৌকার ছইয়ের ভিতরে বসে তিনি লিখে গিয়েছেন দিনগত বৃত্তান্ত।
দু’বছর বয়সে প্রয়াত হন বিশ্বনাথের বাবা রামজয় মুখোপাধ্যায়। মা সরস্বতী বিশ্বনাথকে নিয়ে চলে আসেন হুগলির জিরাটে। সরস্বতী ছেলের বিয়ে দেন বর্ধমানের রাজপণ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে ব্রহ্মময়ীর। স্ত্রী, চার ছেলে, এক মেয়ের ভরা সংসারে মন বসত না বিশ্বনাথের। ছোট থেকে অর্থ উপার্জন করলেও তিনি ছিলেন উদার, পরদুঃখকাতর, দানশীল। যা আয় করতেন সবই খরচ করে ফেলতেন। ফলে মেয়ের বিয়ে দিতে বিস্তর ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। তবুও সন্তানদের শিক্ষায় কোনও খামতি রাখেননি। বিশ্বনাথের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন কলকাতার নামী এমবি ডাক্তার। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর বেশ কয়েকটি বই লেখা ছাড়াও বাল্মীকি রামায়ণের কাব্যানুবাদ করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
বিশ্বনাথের রুট ম্যাপে রক্তজালির মতো অজস্র নদী। তার মধ্যে ভাগীরথী, ইছামতী, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, যমুনার মতো কুলীন নদীর সঙ্গে শাখা-প্রশাখার মতো বিছিয়ে রয়েছে সহস্র খাঁড়িপথ। অধুনা পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে যাত্রা শুরু করে বিশ্বনাথ নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, সেকালের অন্যতম বড় বন্দর সেরাজগঞ্জ হয়ে অসম ছুঁয়ে দূর থেকে সিলেটের পাহাড় দেখে রংপুর পৌঁছেছিলেন। তাঁর যাত্রা শুরুর দিনটি ছিল ১২৪৭-এর ১৫ কার্তিক। সঙ্গী মাঝির নাম বেঙ্গু। তার আগে ২৭ আশ্বিন তিনি জিরাট থেকে অম্বিকা কালনা এসে পৌঁছেছিলেন। যাত্রা শুরুর বর্ণনা — শ্রী শ্রী হরি সহায়ঃ ১২৪৭ সাল ১৫ কার্ত্তিক মোং কালনার গঞ্জ হইতে শ্রী তিলকচন্দ্র কুণ্ডুর তহবিলের শ্রী বেঙ্গু মাজির নৌকায় আরোহন হইয়া ওই দিবস আন্দাজ দিবা এক প্রহরের সময় নৌকা খুলিয়া রাত্র আন্দাজ ছয় দণ্ডের সময় মোং শ্রীপাট নবদ্বীপের পূর্ব আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ দূরে নৌকা লাগান হইল তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে থাকা গেল ইতি।
বিশ্বনাথের ভ্রমণ বিবরণ যে কতটা তথ্যসমৃদ্ধ, পুঙ্খানুপুঙ্খ তার হদিস মেলে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথনির্দেশেই। যাত্রা শুরু করে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর পেরিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন নবাবের খাসতালুকে। তিনি লিখছেন —
‘২১ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অতি পৃর্ত্তুসে নৌকা খুলিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ ছয় দণ্ডের সময় মোং বালাটুঙ্গির বন্দর ও পুলিশের থানার কাছারি দক্ষীণভাগে রাখিয়া মোং বাটীকাপাড়া বাম ভাগে রাখিয়া মোং টীয়াকাটার বন্দরের পূর্ব্ব পারে সন্ধ্যায় সময় নৌকা লাগান হইল রাত্রে তথায় পাক করিয়া থাকা গেল ইতি।
২২ কার্ত্তিক ষুক্রবার অতি প্রাতে নৌকা খুলিয়া মোং মধুপুর বাম ভাগে ও ফিদকাটী বাম ভাগে রাখিয়া উহার উজানে রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সময়ে নৌকা রহিল তথায় রাত্রে পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি।
২৩ কার্ত্তিক শনিবার অতি পৃর্ত্তুসে নৌকা খুলিয়া মোং বাগাডাঙ্গা ও সম্বলপুর বামদিকে রাখিয়া সহর মুরসীদাবাদের শ্রীযুত নওবাব সাহেবের কাটাকাল বাহিয়া পুনরায় ঐ খড়িয়া নদি দিয়া আসীয়া মোং চোড়াদহ ও করিমপুর বামভাগে রাখিয়া মোকাম কুকীনার খালের মোহানা বামভাগে রাখিয়া ঐ খড়িয়া নদিতে রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সময় নৌকা লাগান হইল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি।
২৭ কার্তিক বুধবার। রাতের আঁধার কাটতে তখনও আন্দাজ আড়াই ঘণ্টা বাকি। বিশ্বনাথের যাত্রা শুরু হল। পাবনা নদীর দুই তীরে অনেক গ্রাম। দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁরা পৌঁছলেন ধুনিয়াড়া নীলকুঠিতে। ওয়াস্টিন সাহেবের সেই নীলকুঠির নীচে বহমান নদীর নাম ইছামতী। নৌকা ভিড়িয়ে রাত্রিবাস। পরদিন ইছামতী গাঙ ধরে গিয়ে বড়াল নদীর মোহনার পূর্ব পাড়ে রাত্রিবাস। পরদিন সকালে বড়াল নদীকে ডানহাতে এবং ঢাকা যাওয়ার নদীকে পুব দিকে রেখে বেলকুঠির গাঙ ধরে উত্তরমুখো পথ। বাঁ হাতে পড়ে থাকল সাজাতপুর গ্রাম। এই গ্রামে নৌকা তৈরি হয়। নদীর দুই পাশে বিস্তীর্ণ চর। চাষাবাদের যোগ্য জমি পড়ে রয়েছে প্রচুর কিন্তু লোকাভাব। এখানে নৌকা বেঁধে রাত্রিবাস করতে গিয়ে পোকার ভয়ঙ্কর অতাচার সহ্য করতে হল বিশ্বনাথকে। রাতের খাওয়াও ঠিক করে হল না। তিনি লিখছেন, ‘নৌকা রাখিয়া রাত্রে অতিসয় কিটের উৎপাতকারণ সির্দ্দপক্য করিয়া আহার করা গেল।’
১ অগ্রহায়ণ রবিবার। বিশ্বনাথের নদী ভ্রমণের পক্ষকাল পূর্ণ হল। বেলকুঠির গাঙ বেয়ে সয়দাবাদের গাঙ। তার পশ্চিম দিকে ধানবন্দির খাল। এখানে দু’পাড়েই জনবসতি। দুপুরে বিশ্বনাথ পৌঁছলেন সেরাজগঞ্জে। দেশের মধ্যে সেরাজগঞ্জ বড় বন্দর। সেখানে প্রচুর আমদানি-রপ্তানি হয়। সেখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে বিশ্বনাথ নৌকা বাঁধলেন বন্দরের উত্তর দিকে। সেখান থেকে প্রবাহিত নদীর নাম যমুনা। এই নদী সম্পর্কে বিশ্বনাথের বর্ণনা—‘এখানকার জমুনা নদি বড় পরিসর মধ্যে ২ গঙ্গা অপিক্ষায় অধিক পরিসর বোধ হয় কিন্তু বিস্তর চর পড়িয়াছে রাত্রে তথায় নৌকায় থাকা গেল ইতি।’
৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার। খুব সকালে যমুনা নদী ধরে পুব দিকে পাড়ি দিলেন বিশ্বনাথ। নদীর পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে আরেকটি বড় নদী, দাকোপা। বর্ষায় এই নদীতে প্রচুর জল, তখন নৌকা চলে। শীতে খটখটে। যমুনার পুব দিক ধরে গিয়ে একটি পাহাড়ের নীচে রাত্রিবাস করলেন বিশ্বনাথ। পাহাড় অর্থাৎ বিশ্বনাথ তখন পৌঁছে গিয়েছেন পার্বত্য সিলেট বা অসমের গায়ে। এর পরের বর্ণনায় তা আরও স্পষ্ট হবে।
পরদিন দুপুরে যমুনা হয়ে বিশ্বনাথ এসে পড়লেন ব্রহ্মপুত্র নদে। ব্রহ্মপুত্রে প্রবল স্রোত। কিছুদূর সেই স্রোত ঠেলে বিশ্বনাথ ফের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বাংলার দিকে এসে ধরলেন সেই দাকোপা নদী। বিশ্বনাথ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। অমন বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথেও তিনি একাদশী ব্রত পালন করেছেন। ৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, একাদশী তিথি। বিশ্বনাথ লিখছেন, ‘সন্ধ্যার সময় এক চড়ার নীচে নৌকা থাকীল তথায় রুটী করিয়া একাদসীর অনুকল্প করা গেল এবং রাত্রে তথায় নৌকায় থাকা গেল ইতি।’ এরপর অসম ও উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল ও বন্যজন্তুর আভাস মেলে বিশ্বনাথের লেখায়। ৬ অগ্রহায়ণ শুক্রবার। দাকোপা নদী ধরে নৌকার পাল তুলে তিনি গেলেন উত্তর মুখে। সেখানে চরায় ঘন জঙ্গল। বাঘ ও অন্যান্য জন্তুর ভয় রয়েছে তাই তিনি জঙ্গলের দিকে না গিয়ে নদীর উত্তর-পশ্চিম পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। এখানে তিনি লিখছেন, ‘দাকোপা নদি বাহিয়া পচ্চীম মুখে কতদূর জাওয়া গেল নৌকায় পাইল দিয়া জাওয়াতে উত্তর তরপ এক বিরদ চড়া দেখা গেল তাহাতে কসাড় ও ঝাউ ইত্যাদি অনেক বন আছে ঐ জঙ্গলে ব্যার্ঘ্র ইত্যাদি পষুভয় আছে ঐ জঙ্গল ও ঐ মোহানা উত্তর দিকে রাখিয়া জঙ্গলের পথে না জাইয়া পচ্চীম উত্তরের মোহানা বাহিয়া জাইয়া দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় এক চড়ার নিচে পাক করিয়া আহার করা গেল আগেকার চড়ার নিচে দিয়ে গুন টানিয়া জাইতে মাল্লা লোকেরা বাঘের পায়ের অনেক বড় ২ চিন্ন দেখিলেক জেখানে মধ্যাহ্নে পাক করা গেল সে চড়াতেও জঙ্গলাছে তাহাতেও পষুভয় ইত্যাদি আছে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া জাওয়া গেল সন্ধ্যার সময় পাড়ি দিয়া আসীয়া পাক করিয়া রাত্রে আহার করিয়া থাকা গেল ইতি।’
পরদিন দাকোপা নদী থেকে ফের ব্রহ্মপুত্র নদে এসে পড়লেন বিশ্বনাথ। ব্রহ্মপুত্রের পূব দিকে রাঙা মাটির বড় পাহাড়। পাহাড়ে নানা বৃক্ষাদি। পাথরের পাহাড়ও দেখা যায়। ওই পাহাড় ছিলাটের (সিলেট) পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। এবার ব্রহ্মপুত্রকে উত্তরে রেখে পশ্চিমে তিস্তা নদীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন তিনি। দুপুরে মোহনগঞ্জে আহার করলেন বিশ্বনাথ। সেখানে পাতিলদহ পরগনার কাছারিতে এক তহশিলদার ও মুহুরি থাকেন। মুহুরির সঙ্গে বিশ্বনাথ কথা বলে জানলেন কলকাতার গোপীমোহন ঠাকুরের জমিদারি এটা। হস্তবুদ প্রায় দু’লক্ষ ১১ হাজার টাকা।
এর পর ১২ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত তিস্তা ধরে ভেসে বেড়ালেন বিশ্বনাথ। ১৩ অগ্রহায়ণ বেলা দেড়টা নাগাদ ছালাবাগের বন্দরে নৌকা থেকে নামলেন তিনি। বন্দর ঘুরে সেখানেই রাত কাটালেন। পরদিন ১৪ অগ্রহায়ণ সকালে ছালাবাগে রবিলোচন দাস নামে এক রাজবংশীর বলদ ভাড়া করে জিনিসপত্র চাপিয়ে আন্দাজ দুপুর আড়াইটে নাগাদ রংপুরের দেওয়ানটুলিতে রাজা গোবিন্দপ্রসাদ বসুর সঙ্গে দেখা করলেন বিশ্বনাথ। এখানেই বিশ্বনাথের ৩০ দিনের জলযাত্রার সমাপ্তি। সমাপ্তি বাংলা গদ্যে প্রথম ভ্রমণ-কথার। বলা বাহুল্য, প্রায় দুশো বছর আগে বিশ্বনাথের যাত্রাপথের অধিকাংশ নদীই আজ তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গিয়েছে একসময়ের কোলাহলপ্রিয় বহু বন্দর। হারিয়ে গিয়েছে বহু গ্রাম, জনপদ। তৎকালীন বাংলা গদ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভ্রমণপথের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তা কিন্তু মুছে ফেলা যাবে না। ইতিহাসের এক মহার্ঘ্য ভূ-প্রাকৃতিক দলিল হিসেবেই তা রয়ে যাবে।
(২)
জিন এমন এক অদৃশ্য শক্তি যার রহস্যের পরিসীমা নেই। এর উত্থান পতনে নেই কোনও নির্দিষ্ট ব্যকরণ। কিন্তু যখন আসবে, সঞ্চারিত করবে, বীজ বুনে দেবে পরবর্তী প্রজন্মে তখন ভাসিয়ে দেবে এ কূল ও কূল। দ্বারকানাথ থেকে দেবেন্দ্রনাথ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর থেকে সুকুমার হয়ে সত্যজিৎ, বিশ্বনাথ থেকে আশুতোষ হয়ে উমাপ্রসাদ, এসবই জিনের উথালপাথাল ঢেউ। যে ঢেউয়ে ভেসেছে বঙ্গভূমি।
বাঙালিকে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনায় তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন উমাপ্রসাদ। হিমালয়ের পথ-প্রান্তর, অলি-গলি তিনি চিনিয়েছিলেন। আর মাত্র ১২ বছর পর তাঁর কৈলাস-মানসসরোবর ঐতিহাসিক ভ্রমণের শতবর্ষ। ১৯৩৪-এ পদব্রজে তিনি যাত্রা করেছিলেন হিমালয়ের দুর্গম গিরি ও তিব্বতের কান্তার মরু অতিক্রম করে কৈলাস-মানসের উদ্দেশে। কিন্তু হে পাঠক, এই শেষাংশ তাঁর সেই অভিযান বর্ণনার জন্য নয়। মানসসরোবর নিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা শুধু আপনাদের শোনাতে চাই। পাঠক দয়া করে শুনুন।
ওই অভিযানের বহু বছর পরে উমাপ্রসাদ বইটি লেখায় মনোনিবেশ করেন। তিনি চেয়েছিলেন, বইয়ে পরিশিষ্ট হিসেবে মানসসরোবরে পূর্ববর্তী পর্যটকদের লিখিত কিছু প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনির একটি তালিকা সেখানে সংযোজিত হোক। পুঁথি-পত্র ঘেঁটে তিনি দেখলেন, তাঁরও ১৬ বছর আগে দুই বাঙালি কৈলাস-মানস যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা হলেন প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সত্যচরণ শাস্ত্রী। তালিকা যখন গুটিয়ে এনেছেন তখন আচমকাই অমৃত পত্রিকায় এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক প্রবন্ধে চোখ পড়ল উমাপ্রসাদের। বিস্মিত উমাপ্রসাদ দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে, ওই সাহিত্যিকের মাতামহ সেই ১৮৯৮-এ পদব্রজে সফল অভিযান করেছিলেন কৈলাস-মানসসরোবরে। শুধু অভিযানই নয়, তৎকালীন ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে সেই কাহিনি লিখেও গিয়েছিলেন তিনি। উমাপ্রসাদ লিখছেন, ‘জানি না বাংলা ভাষায় রচিত এর চেয়ে প্রচীনতর কৈলাস-মানস ভ্রমণ বিবরণ মুদ্রিত আকারে আছে কিনা।’
সুপণ্ডিত সেই অভিযাত্রীর আরেকটি পরিচয়ও ছিল। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের নয়নের মণি। একমাত্র তাঁর কথা কিছুটা হলেও শুনতেন দামাল কবি। সেই মহাপুরুষের নাম স্বামী রামানন্দ ভারতী। আর সেই সাহিত্যিকের নাম? লীলা মজুমদার।
বললাম না, জিন আসলে একটা জিনিস!
বিশেষ কৃতজ্ঞতা— অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়



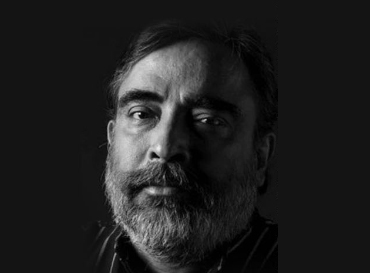
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How