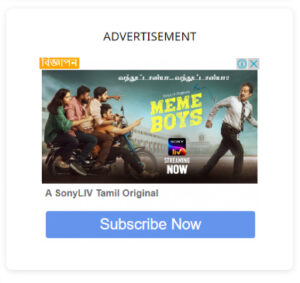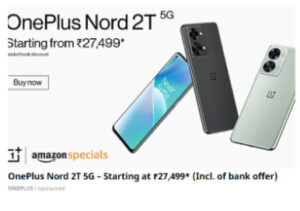- August 13th, 2022
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন (দ্বিতীয় পর্ব)
পূর্ণকুম্ভ, শূন্য মন
সুমন চট্টোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় পর্ব)
সস্ত্রীক কলকাতা থেকে কালকূট দিল্লিতে এসেছিলেন হরিদ্বার যাত্রার দু’দিন আগেই। হয় তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন, নয় আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। কুম্ভে যাব বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে এ ভাবে দিল্লিতে বসে থাকাটা যে তাঁর আদৌ পছন্দ হয়নি, হরিদ্বারে গিয়েই দ্বিতীয় কিস্তিতে সে কথা লিখেছিলেন কালকূট। ‘মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটা কথা ভেবে। দিল্লিতে দুটো দিন কেবল শুয়ে-বসে, হাই তুলে কাটিয়েছি। অথচ তা কাটাবার কথা ছিল না। অন্তত আমার তো জানা ছিল সেই দুটো দিন যদি এখানে এসে কাটাতে পারতাম, তাহলে…।’
দু’দিন আগে গেলেও যে ইতরবিশেষ কিছু হত না, সে কথাও তিনি পরের পংক্তিতেই স্বীকার করেছিলেন। আসলে ‘চলার নামের মদ খেয়ে’ কালকূট তখন মাতাল। ‘বেরুবার জন্য মন অস্থির।’ নিজের পাগল রূপটি দেখে হৃদয়ে প্রায় শিশুর মতো ব্যাকুল। মনের বুকে কান পেতে তখন তিনি শুধুই শুনছেন— ‘চলো চলো।’
যাত্রার দিন অর্থাৎ ৭ এপ্রিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ি নিয়ে রাজধানীর পূর্বী মার্গের অতিথিশালায় পৌঁছতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। একেই দু’দিন কেটেছে অলস বিশ্রামে, তার পরে আবার গাড়ি আসতে দেরি? ভেবেছিলাম বলবেন, ‘গুড মর্নিং।’ উল্টে মুখ ঝামটা দিয়ে শুনিয়ে দিলেন দুটো গালমন্দ। ‘সময় দিয়ে সময় না রাখাটা আমার ঘোরতর অপছন্দ।’ যাত্রার মুখে কালকূটের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে গিয়ে লাভ নেই। বিশেষ করে সেই যাত্রা যদি অমৃত কুম্ভের সন্ধানে হয়।
উপলক্ষ্য একই। কিন্তু বত্রিশ বছরের ব্যবধানে দুই যাত্রায় আসমান-জমিন তফাত। অতএব ভিতরের সঙ্গে বাইরের একটা ঘোরতর টানাটানি চলছিল যেন প্রথম থেকেই। বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না, সমরেশদার অস্থিরতা কেন, এবং কোথায়।
মাত্র ৩০০ টাকা পকেটে নিয়ে, কুম্ভে যাবেন বলে, ‘পিঠে ঝোলা’ আর ‘হাতে ঝুলি’ নিয়ে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে গাদাগাদি-ভিড় ট্রেনের কামরায় উঠে পড়েছিলেন কালকূট। বত্রিশ বছর আগে। কেমন ছিল সেই কামরার চেহারা? ‘এক ফালি ছোট কামরায় জনা আটেকের বসার জায়গা। কলকাতাবাসী এক উত্তরপ্রদেশের ছ’জনের পরিবার বসেছেন প্রায় দুটো সিট দখল করে। আমিও পেয়েছি খানিকটা। আরও জনা চারেক উপরে-নীচে। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।’ ‘লক্ষ-হৃদি-কুম্ভ সায়রে ডুব’ দেবেন বলে সেদিন কালকূট বেরিয়েছিলেন একা। ‘নির্ভয় শক্তির পথে নির্ভয়ে।’
আর বত্রিশ বছর পরে সে দিন? ঝকঝকে মার্ক-ফোর অ্যামবাসাডর গাড়ি, কারণ কালকূটের মন চললেও পা চলে না আর। সঙ্গী সহধর্মিণী-সহ আমরা তিন জন। হাতে পিঠে কালকূটের ঝোলা নেই। ভি-আই-পি আগমার্কা বাক্স গাড়ির ডিকিতে। পকেটে সিগারেটের বদলে হৃদয়ে ছোবল সামলানোর ওষুধ ‘সরবিট্রেট’। ‘কী করব বলো, বত্রিশ বছর পরে আজ আমি তোমাদের হাতের অসহায় শিকার।’
প্রথম যাত্রায় ভিড়ে ঠাসাঠাসি ওই তৃতীয় শ্রেণির কামরায় সহযাত্রীর অনুরোধে দরজা পাহারা দেওয়ার কাজ নিয়েছিলেন কালকূট। ‘সকলে নিদ্রামগ্ন, আমি প্রহরী।’ ‘প্রয়াগ সঙ্গমে লক্ষজনের বিচিত্র রূপ বিচিত্র নদে’ ওই ট্রেনে বসেই যখন তাঁর ‘ধমনীকে ডাক’ দিয়ে চলেছে, সামনে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, ‘একটা কম্বলের পুঁটলি থেকে শীর্ণ, কঙ্কালসার কম্পিত দু’টি হাত একটা কমলালেবু ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। কুম্ভযোগে সঙ্গমে স্নান করলে তার ওই মারাত্মক রোগও সেরে যাবে, এই আশায়, রক্তবমি করতে করতেও ট্রেনে উঠে পড়েছিল কলকাতার কারখানার এই অসুস্থ দেহাতি জনমজুর। ট্রেন যথাসময়ে এলাহাবাদে পৌঁছেছিল ঠিকই। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাওয়া ওই কঙ্কালের শরীর নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাঝপথে মোকামাঘাট স্টেশনে। ‘শত বছর পরমায়ু-সন্ধানী’ সেই অমৃত কুম্ভের যাত্রীকে দেখে কালকূটের মনে হয়েছিল, ‘গাড়ি কি তবে পথ ভুল করেছে।’
ওই মুমূর্ষু সহযাত্রীর জন্য মাঝরাতে গাড়ির গার্ডকে বলে ডাক্তারের খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের কামরায় তাঁর আসনটি খুইয়েছিলেন কালকূট। মাঝরাতের ট্রেনে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলেন একটি প্রথম শ্রেণির কামরায়, যেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে গিয়েছিল, ‘অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ‘অভিশপ্ত’ পরিবারের’। এই পরিবারের তিন ভাইই ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁদের অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু সন্তানের অভাবে তাঁরা সর্বহারা হয়েছিলেন। কালকূটের সঙ্গে আড্ডা জমে যাওয়ার পরে পরিবারের বড় ভাই নিচু গলায় বলেছিলেন, ‘জানেন, প্রয়াগের আর এক নাম তীর্থরাজ। এই বারই আমাদের শেষ, আশা-নিরাশার পরীক্ষার দিন শেষ হয়ে আসছে। এই বারই আমাদের সব সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে, সংসার পাতবে আমার ভাইয়েরা আর আমার…।’
পায়ের তলাতেই কামরার মেঝের উপর বুকে ভর দিয়ে শুয়েছিল লুলা বলরাম, নদে জেলার আমঘাটায়, নক্ষিদাসীর আখড়ার মূল গায়েন। কথায় কথায় গলা ছেড়ে গান ধরেছিল সে — ‘ওগো আইসবে বলে পথের মাঝে জীবন কেটে গেল/ তুমি এমনই খেলা খেল/ সবুর মেওয়া রইল মাথায়/ চইলব এ বার যথায় তথায়/ রোদ বৃষ্টি আশীর্বাদী/ আমার মাথায় ঢেলো।’ মা-খেকো বলার মিষ্টি গলায় এই গান শুনে কালকূটের মনে পড়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সেই গান— ‘কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে/ আমি চলব বাহিরে/ শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে/ আর সময় নাহি রে।’ পদকর্তার নাম শুনে ‘আলোয় আলো হয়ে উঠল বলরামের চোখ। র-বি ঠাকুর! ঠাকুর তো বটেই, রবিও বটে। তা উনি কোথাকার বাউল বাবু?’
প্রয়াগ কুম্ভে ফিরে ফিরে বারে বারে ওই লুলা বলরামের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কালকূটের। আর দেখা হয়েছিল শ্যামার সঙ্গে, অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামী আর সতীনকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামাও উঠেছিল ওই ট্রেনের কামরাতেই। সঙ্গম থেকে ফেরেনি বলরাম, আর শ্যামা ফিরেছিল সিঁথির সিঁদুর খুইয়ে। ফেরার পথেও একই কামরায় আবার। কালকূটের কাঁধে হাত রেখে শ্যামা বলেছিল, ‘এই নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?’ কালকূট, ‘থাকবে।’ শ্যামা, ‘মিথ্যুক, তুমি বড় মিথ্যুক।’
আর এ বার— ‘কোথায় সেই মুমূর্ষু যক্ষ্মারোগী’, অন্ধ্রপ্রদেশের অভিশপ্ত পরিবার, ‘লুলা বলরাম কিংবা শ্যামা’, কোথায় সেই পদে পদে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়, পায়ে পায়ে অভিজ্ঞতা, কেউ বাঁচতে চায়, কেউ সন্তান পেতে চায়, আবার কেউ বা শুধুই গান গেয়ে যেতে!’
কুম্ভ উপলক্ষ্যে নতুন পিচের মোরাম-ঢালা মখমলের মতো রাস্তায় আমাদের দুধ-সাদা অ্যামবাসাডর চলেছে শনশনিয়ে। ওঠা-নামা নেই, ভিড়, ধস্তাধস্তি, পলে পলে জীবনের সঙ্গে ঘর্ষণ নেই। মোদীনগর পেরোতেই চেখে পড়ল বাস আর ট্র্যাক্টর বোঝাই হয়ে হাজারে হাজারে পুণ্যার্থী চলেছেন হরিদ্বারের গঙ্গাদ্বারে। তাদের মধ্যে একজনও লুলা বলরাম কিংবা শ্যামা ছিল না? হয়তো ছিল। কিন্তু কালকূটের সঙ্গে তাদের পরিচয় হল কই? এ বারের যাত্রায় রোগী স্বয়ং কালকূট। আমরা প্রহরী। আমাদের তিন জনকে বাদ দিয়ে কালকূটের সঙ্গী বত্রিশ বছর আগের সেই অভিজ্ঞতা। কাঁধের শৌখিন শান্তিনিকেতনী ঝোলায় ‘গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা আর অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’-র অষ্টাদশ সংস্করণ।
বত্রিশ বছর আগে প্রয়াগের মেলায় প্রথম রাত্তিরে এক চিলতে মাথা গোঁজার জায়গা পেতে অপরিচিতের অপমান হজম করে কতখানি কৃচ্ছ্রসাধন কালকূটকে করতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা আছে ওই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। রাত কাবার করে খুব সকালে ট্রেন পৌঁছয় এলাহাবাদ স্টেশনে। স্টেশন থেকে বেরোবার মুখে নিতে হল মহামারীর ইঞ্জেকশন। ইঞ্জেকশন নেওয়াকে কেন্দ্র করে নিরক্ষর তীর্থযাত্রীদের সে কী বচসা নিজেদের মধ্যে! তার পর তিনগুণ ভাড়া দিয়ে রিকশায় করে আপাদমস্তক ধুলোয় ডুবিয়ে গঙ্গার বাঁধ পর্যন্ত। তার পর গোরু খোঁজার মতো, মাথা গোঁজার আশ্রয়ের সন্ধান। এনকোয়ারি অফিসে গিয়ে কোনও ফল হল না। সেখান থেকে বেরিয়ে কালকূট দেখলেন, স্টেশনে ইঞ্জেকশন নিয়ে বচসা করতে দেখা এক দিদিমা তাঁর দুই ভাইপোকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পায়ে পায়ে। উপায়ান্তর না থাকায় অতএব লজ্জার মাথা খেয়ে, তাঁদের পিছু নেওয়া। কিছু দূর সঙ্গে যাওয়ার পরেই বড় ভাইপো টের পেয়ে গেলেন কালকূটের মতলব। ‘যাক ওসব চালাকি ঢের দেখেছি, এখন কেটে পড়ো।’
কিন্তু ওই রাতে কেটে কালকূট যাবেন কোথায়? তীর্থস্থানে কুকুর-বেড়ালকেও তাড়াতে নেই। অতএব ভাইপো পাঁচুগোপালের ক্রুদ্ধ মন্তব্য ‘ভেটো’ করে দিলেন দিদিমা। শেষ পর্যন্ত ওই দিদিমারই দাক্ষিণ্যে মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছিল বাঙালি বোষ্টমদের আখড়ায়। ‘তাঁবুর মাঝখান দিয়ে ভাগাভাগি করে এক-একটি পরিবারের আস্তানা করা হয়েছে। মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে বিচুলি। ব্যবস্থা আছে ইলেকট্রিক আলোর। সত্যিই বাড়ির মতোই ব্যবস্থা বটে।’ অসুবিধে ছিল একটাই। তীর্থস্থানের ধুলো ধুয়ে ফেলতে গায়ে সাবান মাখতে দেননি দিদিমা। সাবান হাতে স্নান করতে কালকূট কলতলায় যাচ্ছেন দেখে ‘তাঁবু কাঁপিয়ে খরখর করে’ দিদিমা বলে উঠেছিলেন, ‘এ কী ম্লেচ্ছ কাণ্ড গো বাবা। প্যান্ট পরে ইঞ্জিশন না হয় নিয়ে এলে, নইলে ছাড়বে না। কিন্তু দেবতার থানে সাবাঙ্ মাখতে যাচ্ছো কী বলে। তীর্থক্ষেত্রে তেল-সাবাঙে অপবিত্র হয়, তাও জানো না বাছা।’
বত্রিশ বছর পরে দিদিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও কথা ছিল না কালকূটের। হলেও এ বারও নির্ঘাত তিনি আঁতকে উঠতেন। কালকূটের ভি-আই-পিতে এ বার সুগন্ধী সাবান তো ছিলই, ছিল গোটা তিনেক স্কচ হুইস্কির বোতলও। হরিদ্বারে মদ্যপান নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ এমনকী হোটেলের ঘরেও। কিন্তু ডাক্তারের বারংবার নিষেধের তোয়াক্কা করেন না যে কালকূট, তাঁকে নিরস্ত করবে বীর বাহাদুর সরকারের বোকা-বোকা নিষেধাজ্ঞা? রাজ রাতে নৈশাহারের আগে হোটেলের ঘরের জানালার পাশে বসে পুণ্যলোভাতুর জনতার অবিরাম মিছিল দেখতে দেখতে পানীয় বিষের পাত্রে চুমুক দিতেন কালকূট। ‘আমি তো পুণ্য সঞ্চয়ের কথা ভেবে আসিনি! মত্তে আসিনি তীর্থ নিয়ে। আমি চলব আমার নিয়মে।’ সত্যিই কি তাই? থাক সে কথা এখন। (চলবে)


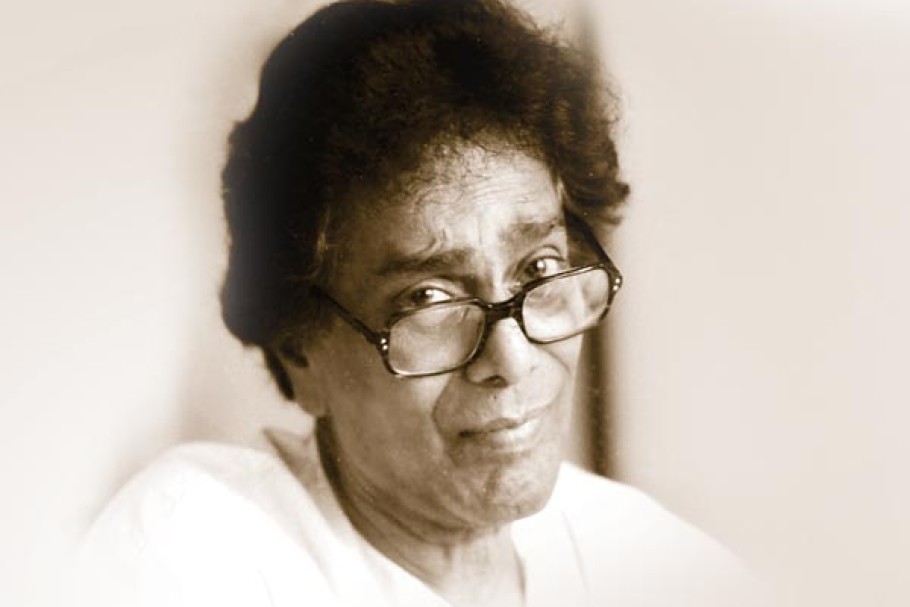
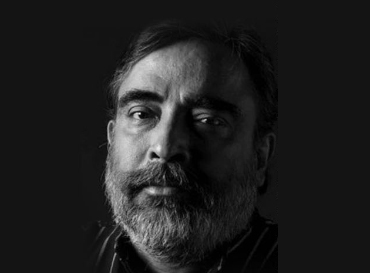
 Arts and Literature
Arts and Literature Bioscope
Bioscope Columns
Columns Green Field
Green Field Health World
Health World Interviews
Interviews Investigation
Investigation Live Life King Size
Live Life King Size Man-Woman
Man-Woman Memoir
Memoir Mind Matters
Mind Matters News
News No Harm Knowing
No Harm Knowing Personal History
Personal History Real Simple
Real Simple Save to Live
Save to Live Suman Nama
Suman Nama Today in History
Today in History Translation
Translation Trivia
Trivia Who Why What How
Who Why What How